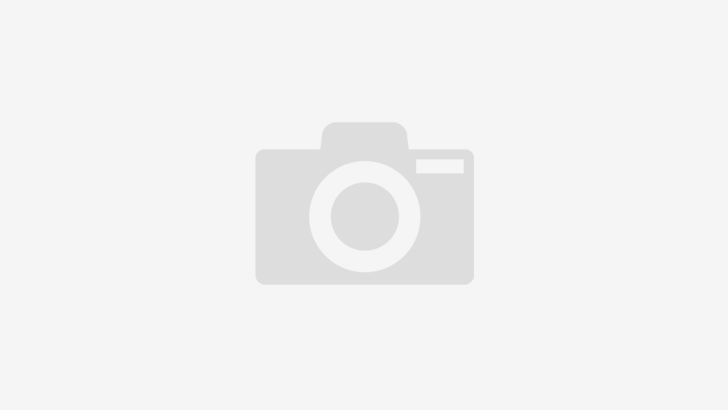১১ মে ২০২৫, ৪:৪৮:৪০
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সকল জোট কয়েকদিন আন্দোলন করে শেষমেশ আওয়ামী লীগকে নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এটাই কি সব সমস্যার সমাধান করবে? আওয়ামী লীগ কি এভাবে বিলীন হয়ে যাবে?

সম্পাদকীয়: বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের জটিল প্রশ্ন
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে একটি চাঞ্চল্যকর দাবি উঠে এসেছে—আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধকরণ। এই দাবি সমাজে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আন্দোলনকারীদের মতে, দলটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে বৈষম্য ও অসমতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। তবে, এই দাবির রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে, দলটির প্রায় দেড় কোটি কর্মী-সমর্থকের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগই সবচেয়ে জরুরি: একটি প্রতিষ্ঠিত দল নিষিদ্ধ হলে লাখো মানুষ কীভাবে হঠাৎ রাজনৈতিক পরিচয় হারাবেন? তাদের পুনর্বাসনের রাস্তাটি কোথায়?
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত—রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে পক্ষপাতদুষ্ট নীতি, সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করা। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের দাবি কতটা বাস্তবসম্মত? আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে জড়িত একটি ঐতিহাসিক দল, যার ভিত্তি শুধু ক্ষমতায় নয়, গণমানুষের মাঝেও প্রোথিত। দলটি নিষিদ্ধ হলে শুধু একটি সংগঠন নয়, একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ্য অবস্থানকেও অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হবে। এতে করে গণতন্ত্রের বহুত্ববাদী চরিত্র ক্ষুণ্ণ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে।
প্রশ্ন উঠেছে, দলটির সমর্থক ও কর্মীরা কোথায় যাবেন? রাজনৈতিক দল কেবল নেতা-কর্মীদের সমষ্টি নয়; এটি লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। একটি দল হঠাৎ নিষিদ্ধ হলে তার সমর্থকদের একটি বড় অংশ হয় রাজনৈতিক শূন্যতায় পড়বেন, নয়তো অন্যান্য দলে ছড়িয়ে যাবেন। প্রথম ক্ষেত্রে, তারা রাষ্ট্রের প্রতি বিমুখ হয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীস্বার্থে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেন, যা সামাজিক অস্থিরতা বাড়াবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বিদ্যমান দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে। এছাড়া, নতুন উগ্রবাদী গোষ্ঠীর জন্ম দেওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।
সমস্যার সমাধান নিষিদ্ধকরণে নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, নীতিনির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে দলটির মাধ্যমে সমর্থকদের আশা-ভরসায় ফেরানো যায়। একইভাবে, বিরোধী দলগুলোর কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সকল দলের জন্য সমান আইনি সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে জনগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী রাজনৈতিক মতাদর্শ বেছে নিতে পারেন।
যেকোনো দল নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে। এটি একটি বিপজ্জনক প্রেসিডেন্ট সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে ভবিষ্যতে কোনো সরকারই বিরোধী মত দমনের হাতিয়ার হিসেবে এই নজির ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে, যা অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে।
বর্তমান সংকটের সমাধান হলো সংলাপ। সরকার, আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র আন্দোলনকারীদের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণের রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য জবাবদিহিতামূলক কাঠামো, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সুশাসন নিশ্চিত করাই স্থায়ী সমাধান। নিষিদ্ধকরণের দাবি আদৌ বাস্তবায়িত হলেও তা অস্থায়ী; স্থায়ী পরিবর্তন আসে সমন্বিত প্রচেষ্টায়।
উপসংহার
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ন্যায্য দাবিকে সমর্থন করেই বলা যায়, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের প্রস্তাব সমস্যার সমাধান নয়, বরং নতুন সংকটের সূত্রপাত। দেড় কোটি মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় মুছে ফেলা কোনো গণতন্ত্রের কাম্য নয়। প্রয়োজন রাষ্ট্রের সকল স্তরে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা, যেখানে নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত এবং রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য।এভাবেই, বাংলাদেশ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।